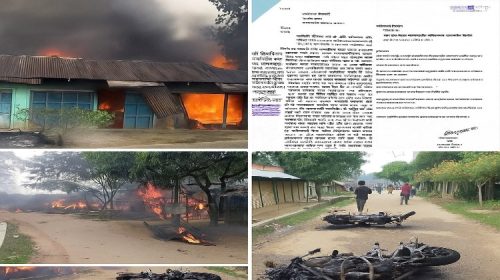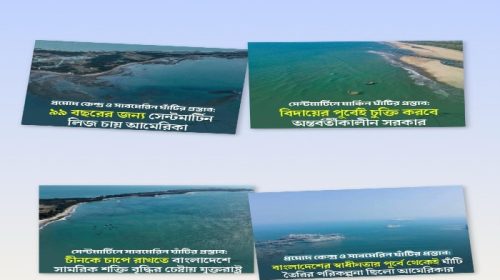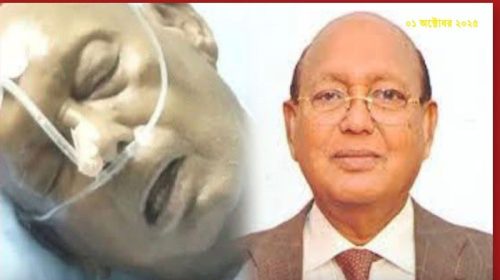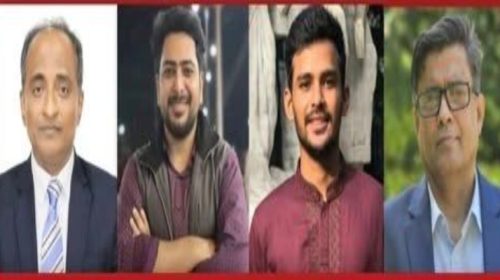সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের দেয়া রায়ের সূত্রেই বাতিল হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা যায়। এজন্য সংসদে একটি ছোট্ট বিল উত্থাপন করে তা পাশ করিয়ে নিলেই হয়। বিশ্লেষকগণ মনে করেন, এবিষয়ে কোনো জটিলতা থাকার কথা নয়। এক্ষেত্রে যেমন পূর্বেই সর্বক্ষেত্রেই বিপুল ঐকমত্য তৈরি হয়ে আছে, তেমনই এবিষয়ে সংসদীয় অভিজ্ঞতা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনায় প্রশাসনিক দক্ষতাও যথেষ্ট রয়েছে।
২০০৮-এর নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদেরই আন্দোলনের ফসল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধান থেকে মুছে দিতে উদ্যোগী হয়। এর মাধ্যমে দলীয় সরকারের অধীনে যেকোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগের রায়ে সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর ধারাসমূহ বাতিল করা হয়। ওই রায়কে ভিত্তি ধরেই সংবিধান সংশোধন করে মহাজোট সরকার, যাতে বিলুপ্ত হয় নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। যদিও আদালত বলেছিল যে, পরবর্তী দুটি মেয়াদের সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে। এই সূত্রটিকেই কাজে লাগিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বা নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। আর সংসদেও যেহেতু সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেহেতু সংবিধানে তা পুনঃস্থাপনেও কোনো বাধা হবে না।
চার-তিনে বিভক্ত রায়ে ‘তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা’ বিলুপ্ত : ২০১১ সালের ১০ মে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে রায় দেয়ার সময় প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন বিচারপতি খায়রুল হক। রায় প্রদানকারী বাকি ৬ জন বিচারপতির মধ্যে ৩ জন তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ৩ জন দেন ভিন্নমত। রায়ে এই ব্যবস্থার আওতায় পরবর্তী দুটি সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে বলে মত দেয়া হয়। ওই সময় সংক্ষিপ্ত রায়ে সর্বোচ্চ আদালত বলে, বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের বিচারপতিদের বাদ রেখে সংসদ এ সরকার পদ্ধতি সংস্কার করতে পারে।
বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের লেখা রায়ের সঙ্গে একমত হন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন, বিচারপতি এস কে সিনহা ও বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। এই রায়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মত দেন বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিঞা। তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা। তবে বিচারপতি মো. ইমান আলী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মত না দিয়ে বিষয়টি জাতীয় সংসদের ওপর ছেড়ে দেন। অর্থাৎ এই রায়টির পক্ষে ৪ জন এবং বিপক্ষে ৩ জন অভিমত দেন। এটি সর্বসম্মত ছিল না, বরং ছিল বিভক্ত রায়। ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এটি গৃহীত হয়। পরে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করা হয়। এতে বিচারপতিদের মতভিন্নতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। তবে, আগামী দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করা যেতে পারে বলে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের রায়ে যে অভিমত ছিল, পূর্ণাঙ্গ রায়ে তা বহাল থাকে। বিপক্ষে মত প্রদানকারী দুজন বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা ও নাজমুন আরা সুলতানার দৃষ্টিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানসম্মত, গণতান্ত্রিক এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয়। রায়ের পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় পরবর্তী দুটি নির্বাচন এ ব্যবস্থার অধীনে হবে।
আপিল বিভাগের রায়ের পর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা তুলে দেয়া হয়। সংবিধানের এই সংশোধনের বিরোধিতা করে বিএনপিসহ অধিকাংশ বিরোধী দল। তারা বলে, সরকার রায়ের একটি অংশ ধরে সংবিধান সংশোধন করলেও অন্য অংশটি উপেক্ষা করেছে। তারা তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে আসছে। দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি ১৯৯৬ সালে এলেও ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন একটি সরকারের অধীনে হয় সাধারণ নির্বাচন। এরপর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের চাপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান এনে সংবিধান সংশোধন করে বিএনপি। এর আগে ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম সলিম উল্লাহসহ কয়েকজনের রিট আবেদনে ২০০৪ সালে হাইকোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করে। ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে যায় রিট আবেদনকারী পক্ষ।
উচ্চ আদালতে যা ঘটেছিল : দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হলে সেখানেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের পক্ষে সর্বসম্মত মত মেলেনি। উচ্চ আদালতের ৭ জন বিচারপতির মধ্যে ৪ জন বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের পক্ষে রায় দেন এবং ৩ জন ভিন্নমত পোষণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল বলে ঘোষিত হয়। তবে বিচারপতি আবদুল ওয়াহাব মিঞার অভিমতে বলা হয়, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার (ত্রয়োদশ সংশোধনী) সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা হলে নিশ্চিতভাবেই দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এই সংশোধনী সাংবিধানিক অপরিহার্যতা।’ প্রধান বিচারপতি ও তার সঙ্গে সহমত পোষণকারী অপর তিন বিচারপতির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বিচারপতি আবদুল ওয়াহাব মিঞা ১৭৮ পৃষ্ঠার অভিমত দেন। এতে বলা হয়, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার (ত্রয়োদশ সংশোধনী) সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা হলে নিশ্চিতভাবেই দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, যেমনটি হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব পড়বে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশ এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পেছনে চলতে শুরু করবে। গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনে এই ব্যবস্থা মানুষ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। নির্দলীয় সরকারের অধীনেই তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।’ বিচারপতি ওয়াহাবের অভিমতের সঙ্গে বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা একমত পোষণ করেন। আর বিচারপতি মো. ইমান আলী বিষয়টি সংসদের উপর ছেড়ে দেন।
এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিমকোর্টের ৮ জন সিনিয়র আইনজীবীকে এ্যমিকাস কিউরি (আদালতের আইনি সহায়তাকারী) নিযুক্ত করা হয়। এরা হলেন, সাবেক বিচারপতি টি.এইচ খান, সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন, সাবেক এ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, সাবেক এ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. এম জহির, ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দীন মাহমুদ এবং ব্যারিস্টার আজমালুল হক কিউসি। এছাও সরকার পক্ষে ছিলেন এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। একমাত্র ব্যারিস্টার আজমালুল হক ছাড়া অন্য সকলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পক্ষে আইনি ও সাংবিধানিক ব্যাখ্যা আদালতের সামনে উপস্থাপন করেন। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে জড়ানোর বিষয়ে তাদের কারো কারো আপত্তি ছিল। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সঙ্গে তাদের কোনো দ্বিমত বা আপত্তি ছিল না। এমনকি তাদের কেউ কেউ আপিল বিভাগের শুনানিতে বলেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হলে দেশে রাজনৈতিক বিরোধ চরম আকার ধারণ করবে। এতে যে কোনো সময় রাজনৈতিক প্রলয়ও ঘটে যেতে পারে। আর এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ অভিমত তুলে ধরে বলেন, ‘অনির্বাচিত লোক গণতন্ত্রের চর্চা করলে গণতন্ত্রের স্পিরিট নষ্ট হবে, এটা ঠিক নয়।’ আপিল বিভাগের সাত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে নবম দিনের শুনানিতে এ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘জাতির একটি সন্ধিক্ষণে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়। বিতর্কমুক্ত একটি ভোটার তালিকা তৈরি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।’ তিনি বলেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের প্রজাতন্ত্রের ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অবৈধ বলে মন্তব্য করছে, আমি তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এটা করা জরুরি ছিল। কাজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা খারাপ নয়। তবে কিছু লোকের কারণে এটা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির রদবদল করতে হলে তা সংসদ করবে।’ এমনকি আপিল আবেদনকারী আবদুল মান্নান রায় তাঁর পক্ষে যাওয়ায় খুশি হলেও রায়ের দ্বিতীয় অংশ উল্লেখ করে বলেন, ‘দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন এ পদ্ধতিতে হবে।’
বিপুল ঐকমত্য উপেক্ষা : শুরু থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বরাবরই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতি বিপুল ঐকমত্য সাধিত হয়েছে। কি রাজনৈতিক, কি আইনগত আর কি বুদ্ধিবৃত্তিক- সকল দিক দিয়েই এর প্রতি বিপুল জনসমর্থন বিদ্যমান। রাজনৈতিকভাবে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালে দেশে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে একটি রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট, জামায়াতসহ ইসলামপন্থী দলসমূহ, এরশাদের জাতীয় পার্টি প্রভৃতি সকল দল এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথের বিপুল আন্দোলনসহ সর্বময় কর্মকা- চালিয়েছে। এর ফলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপিও এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংসদে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। ফলে এই ব্যবস্থার বিপক্ষে কথা বলার কোন সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না।
অন্যদিকে দেশের শীর্ষ আইনবিদরাও এর পক্ষে একমত রয়েছেন। দেখা যায়, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সম্বলিত ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জনৈক আইনজীবী ১৯৯৮ সালে হাইকোর্টে রিট করলে এর প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট হাইকোর্টের তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ রায় দেন। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বৈধ ঘোষণা করে এই রায়ে বলা হয়, ‘১৯৯৬ সালের ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানসম্মত।’ এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে আপিলকারী ও রাষ্ট্রপক্ষ ছাড়াও শুনানিতে এ্যামিকাস কিউরি (আদালতের আইনি সহায়তাকারী) হিসেবে শীর্ষস্থানীয় আটজনের মধ্যে ৭ জনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। কেবল আজমালুল হোসেন কিউসি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এটা সংবিধানের মৌল কাঠামোর পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন। এমনকি শুনানীকালে সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন।
রায়ের এই অবস্থানের বিষয়ে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারক এবং এ্যামিকাস কিউরিদের ৮ জনের মধ্যে ৭ জন এবং এ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। এছাড়াও গত এপ্রিল-মে-২০১১ মাসে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির উদ্যোগে যে সংলাপের আয়োজন করা হয় সেখানেও রাজনৈতিক নেতা, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, পেশাজীবী প্রভৃতিসহ প্রায় সকলের পক্ষ থেকেই একবাক্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়। এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীও সংশোধিত আকারে এর পক্ষে বক্তব্য দেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আংশিক রায় ঘোষণার পর এই রায়ের প্রথম অংশকে পুঁজি করে পুরো ব্যবস্থাই সংবিধান থেকে তুলে দেয়া হয়। এমনকি এই সংশোধনী সংসদে পাশ করতে গিয়েও নানান নাটকের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বিশ্লেষকরা মনে করেন, এখন ক্ষমতা পেয়ে এই ব্যবস্থাকে সংবিধান থেকে উচ্ছেদ করা বিপুল জনমতের সঙ্গে যুদ্ধ করারই শামিল হবে। একটি জনমত জরিপেও উল্লেখ করা হয়, “নির্দলীয় সরকারের পক্ষে রয়েছেন দেশের ৮২ ভাগ মানুষ।”
সংবিধান সংশোধনী কমিটির সদস্যরা যা বলেছিলেন: ২০১০ সালের ২১ জুলাই প্রথম ১৫ জন সদস্য নিয়ে সংবিধান সংশোধনী কমিটি গঠন করা হয়। তারা ২৭টি বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে ২০১১ সালের ২৯ মার্চ বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হয়। সংবিধান সংশোধনী কমিটির সদস্য (সেসময় এঁরা মন্ত্রী ছিলেন) তোফায়েল আহমেদ বলেছিলেন, “এটা সেটল ইস্যু, এটা পরিবর্তন করার দরকার নেই।” আমির হোসেন আমু বলেন, “তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেভাবে আছে সেভাবেই রাখা উচিত।” রাশেদ খান মেনন বলেন, “তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের দরকার নেই।” ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, “সংবিধানে তিন মাস নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে।” শিরীন শারমিন (বর্তমান স্পিকার) বলেছিলেন, “তত্ত্বাবধায়ক সংশোধনের দরকার নেই।” সাবেক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু বলেন, “এমন কিছু করা ঠিক হবে না যা বিতর্ক সৃষ্টি করে।” কমিটির কো-চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও বলেন, “তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করার দরকার নেই।”
এই বিপুল ঐকমত্য নিয়ে ২৭ এপ্রিল, ২০১১ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংবিধান সংশোধন কমিটির সদস্যরা দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘জনগণ আর অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা দেখতে চায় না।’ ১০ মে কমিটি আবার বলে, ‘শর্ত সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।’ ২৯ মে সংবিধান সংশোধনী কমিটি সর্বম্মতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাখার পক্ষে সুপারিশ করে। এভাবে রাজনৈতিক নেতা, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, পেশাজীবী প্রভৃতিসহ প্রায় সকলের পক্ষ থেকেই একবাক্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়। এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীও সংশোধিত আকারে এর পক্ষে বক্তব্য দেন। ৩০ মে কমিটি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে সবকিছু উল্টে যায়, সবকিছু বদলে যায়। ২০ জুন কমিটি নতুন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করে।
পুনঃস্থাপন হবে ইতিবাচক: দেশের সংবিধানে তত্ত্বাধায়ক বা নিরপেক্ষÑ যে নামেই হোক, এধরনের একটি ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হলে তাতে কোনো সংকট আদৌ তৈরি হবে না বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কেননা এজন্য পূর্ব থেকেই এবিষয়ে বিপুল ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। যাতে খোদ আওয়ামী লীগ ও তাদের শরিকদেরও অংশ আছে। উচ্চ আইন অঙ্গনেও তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লক্ষণীয়। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আছে সংসদীয় অভিজ্ঞতাও।
এধরণের নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সরকার পরিচালনায় দেশের জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও অন্য সকল সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশাসনিক দক্ষতা তৈরি হয়ে আছে। ফলে এটি যেমন নতুন কোনো ‘আবিষ্কার’ বলে গণ্য হবে না তেমনই কোনো সংকটেও পড়তে হবে না।
এবিষয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিশ্লেষক মোবায়দুর রহমান একটি গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করে বলেন, কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার বিষয়ে উচ্চ আদালতের এসব রায় যদি আক্ষরিক অর্থে কার্যকর হয় তাহলে সেদিন সুদূর নয় যেদিন ব্ল্যাকহোলের মতো বাংলাদেশ সাংবিধানিক শূন্যতার বিশাল গহ্বরে পতিত হবে এবং অন্তহীন নৈরাজ্য দেশকে গ্রাস করবে। কেয়ারটেকার অবৈধ হলে সব সরকারই অবৈধ। কেয়ারটেকার ব্যবস্থা যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে সেই কেয়ারটেকারের অধীনে গঠিত সমস্ত সরকারই অবৈধ হয়ে যায়। সেই কেয়ারটেকার সরকার অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে শেখ হাসিনার আমলে জনাব খায়রুল হক হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। এবার এ কেয়ারটেকারের অধীনে গঠিত হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাহলে তার নিয়োগও অবৈধ হয়। তার নিয়োগ যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে তার দেয়া সবগুলো রায় অবৈধ। কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে এই ব্যবস্থার অধীনে যেসব নির্বাচন হয়েছে তার সবগুলোই অবৈধ। ঐসব ইলেকশনের মাধ্যমে যেসব সরকার গঠিত হয়েছে তার সবগুলো সরকারই অবৈধ। তাহলে ১৯৯৬ সালে গঠিত হাসিনার সরকার, ২০০১ সালে গঠিত খালেদা জিয়ার সরকার এবং ২০০৯ সালে গঠিত শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকার- এই ৩টি সরকারই অবৈধ।